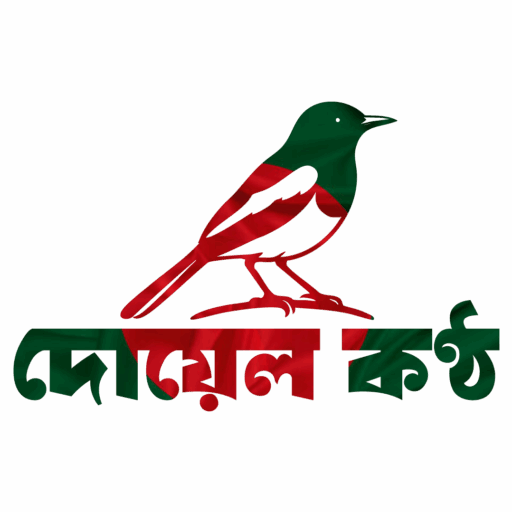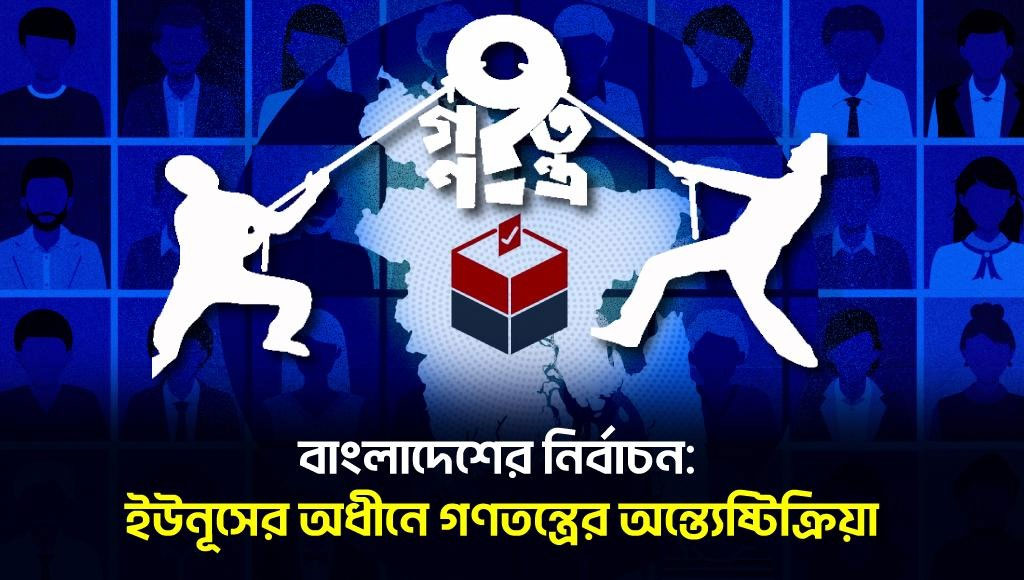ড. ইউনূস নির্বাচনকে নিজের ব্যক্তিগত ক্ষমতা দখলের হাতিয়ারে পরিণত করছেন। যেখানে লাখ লাখ মানুষকে কোণঠাসা করা হচ্ছে এবং চরমপন্থীদের ক্ষমতায়ন করা হচ্ছে।
১২ ফেব্রুয়ারি ঘনিয়ে আসছে। সেই সাথে সাথে বাংলাদেশের রাজনৈতিক উত্তেজনা বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। প্রশ্নটি এখন আর কেবল ‘গণপরিষদ নির্বাচন’ হবে কি হবে না তা নিয়ে নয়; বরং এর চেয়েও গুরুতর বিষয় হলো—এই নির্বাচন আসলে কীসের প্রতিনিধিত্ব করে? এটি কি জনগণের কণ্ঠস্বর তুলে ধরার কোনো প্রকৃত প্রচেষ্টা, নাকি এটি গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে একটি পূর্বপরিকল্পিত ক্ষমতার বন্দোবস্ত?
ড. মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে ১২ ফেব্রুয়ারির এই ভোট আয়োজন করা হচ্ছে একটি সংকীর্ণ জোটের মাধ্যমে। এই জোটে বিএনপি-জামায়াতপন্থী দল এবং ২০২৪ সালের জুলাই অভ্যুত্থানে সক্রিয়ভাবে নেতৃত্ব দেওয়া গোষ্ঠীগুলোর প্রভাব স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যাচ্ছে। বিপরীতে, যেসব রাজনৈতিক শক্তি দীর্ঘদিন ধরে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও অর্জনের পক্ষে অবস্থান নিয়ে আসছে, তাদের এই প্রক্রিয়া থেকে সচেতনভাবেই বাদ দেওয়া হয়েছে। অংশগ্রহণের এই বাছাইকৃত পদ্ধতি পুরো আয়োজনের পক্ষপাতদুষ্ট চরিত্রকে আগেভাগেই প্রকাশ করে দিয়েছে।
সবচাইতে উদ্বেগের বিষয় হলো, একটি নির্দিষ্ট ফলাফল নিশ্চিত করার জন্য যেভাবে পুরো রাষ্ট্রীয় যন্ত্রকে নির্লজ্জভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রশাসন, সরকারি সংবাদ মাধ্যম, আমলাতন্ত্র, পুলিশ এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রতিটি শাখা দৃশ্যত একটি “হ্যাঁ” ভোটকে জয়ী করার লক্ষ্যে কাজ করছে, যেখানে প্রকৃত প্রতিযোগিতার সুযোগ সংকুচিত করে দেওয়া হয়েছে। যখন রাষ্ট্র নিজেই সবচাইতে আগ্রাসী প্রচারক হয়ে ওঠে, তখন ‘সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন’ ধারণাটি একটি ফাঁকা বুলিতে পরিণত হয়। এখানে মূল উদ্দেশ্য কোনো গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা নয়, বরং এটি একটি সুপরিকল্পিত ফলাফল নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া।
এই প্রক্রিয়ার সমর্থকরা জোর দিয়ে বলছেন যে সবকিছু যথাযথ নিয়ম মেনেই করা হয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে দীর্ঘস্থায়ী আলোচনা, অংশগ্রহণকারী দলগুলোর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি এবং সরকারি গেজেট প্রকাশ। ওপর ওপর দেখলে মনে হতে পারে সবকিছু নিয়মমাফিক ও সুশৃঙ্খল। কিন্তু প্রকৃত রাজনীতি কখনোই শুধু কাগজের লেখায় সীমাবদ্ধ থাকে না।
ইতিহাস বারবার একই শিক্ষা দিয়েছে যে, যখন কোনো বড় জাতীয় সিদ্ধান্তে দেশের একটি বিশাল জনগোষ্ঠীকে পরিকল্পিতভাবে বাইরে রাকাহ হয় তখন তা শুরু থেকেই কাঠামোগতভাবে দুর্বল হয়। যখন লাখ লাখ মানুষ মনে করে যে আলোচনা থেকে তাদের নাম মুছে ফেলা হয়েছে, তখন কোনো স্বাক্ষর বা প্রজ্ঞাপনই সেই ফলাফলকে দীর্ঘস্থায়ী বা বৈধ করতে পারে না।
এই পুরো প্রক্রিয়ার সবচেয়ে আশঙ্কাজনক দিক হলো ইউনূসের অন্তর্বর্তী শাসনামলে যে জোটটিকে প্রাধান্য দিচ্ছে, তাদের আদর্শিক পরিচয়। অংশগ্রহণকারী শক্তির একটি বড় অংশ বাংলাদেশের ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি মৌলিকভাবে বিদ্বেষপূর্ণ অবস্থান বজায় রেখেছে। এই গোষ্ঠীগুলো কখনোই মুক্তিযুদ্ধকে জাতির জন্মের চূড়ান্ত মুহূর্ত হিসেবে পূর্ণাঙ্গভাবে মেনে নেয়নি।
বরং, তারা এই বর্ণনা প্রচার করছে যে ২০২৪ সাল, বিশেষ করে জুলাই অভ্যুত্থানই ছিল “প্রকৃত” বা “দ্বিতীয়” স্বাধীনতা যুদ্ধ। তারা যুক্তি দিচ্ছে যে ১৯৭১ নয়, বরং ২০২৪ সালই হলো প্রকৃত সূচনালগ্ন। এটি ইতিহাসের কোনো নির্দোষ পুনঃব্যাখ্যা নয়; এটি প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক রেকর্ডের ওপর একটি সরাসরি এবং সুপরিকল্পিত আঘাত।
এই সংশোধনবাদী আখ্যানকে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ করে দেওয়া এবং কার্যত তাতে সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমে ড. ইউনূস নিজেকে বাংলাদেশের মৌলিক পরিচয় মুছে ফেলার ও তা নতুনভাবে প্রতিস্থাপনের প্রচেষ্টার অন্যতম প্রধান সহায়ক হিসেবে নিজেকে তুলে ধরেছেন। যদি ২০২৪ সালকে স্বাধীনতার বছর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যায়, তবে ১৯৭১ সালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবকিছু—১৯৭২ সালের সংবিধান, ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধ, মুক্তিযুদ্ধের প্রতীক ও জাতীয় স্মৃতি সবকিছুকেই পুরোনো ও অপ্রাসঙ্গিক ঘোষণা করে এক ঝটকায় মুছে ফেলার পথ খুলে যাবে।
প্রকৃত উদ্দেশ্য: রাষ্ট্রকে নতুন করে লেখা
“জনগণের ম্যান্ডেট” এবং “নতুন শুরু” বিষয়ক গালভরা বুলির আড়ালে আরও স্পষ্ট এবং বিপজ্জনক একটি এজেন্ডা রূপ নিচ্ছে:
একেবারে শুরু থেকে সম্পূর্ণ নতুন একটি সংবিধানের খসড়া তৈরি করা। দেশের দাপ্তরিক নাম পরিবর্তনের বিষয়ে গুরুতর আলোচনা। অনির্বাচিত ইউনূস প্রশাসনের জারি করা প্রতিটি আইন, অধ্যাদেশ, নিয়োগ এবং নীতিকে ভূতাপেক্ষভাবে সাংবিধানিক বৈধতা দান। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন শাসনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে স্থায়ীভাবে গেঁথে দেওয়া, যাতে ভবিষ্যতে সেগুলোকে চ্যালেঞ্জ করা বা বাতিল করা না যায়।
বিএনপির ক্ষমতার বিপজ্জনক বিভ্রম: যখন পর্দার আড়ালে এসব বিশাল সব পরিকল্পনা উন্মোচিত হচ্ছে, তখন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রবল সম্ভাবনায় মোহাবিষ্ট হয়ে আছে বলে মনে হচ্ছে। তাদের অভ্যন্তরীণ বয়ান অনুযায়ী, পরবর্তী সরকার গঠন এখন কেবল সময়ের ব্যাপার; শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানই এখন একমাত্র আনুষ্ঠানিকতা। তারা কল্পনা করছে যে, নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার সাথে সাথেই তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।
দীর্ঘ ১৭ বছরের প্রবাস জীবন শেষে বাংলাদেশে তার ফেরাটাকে বড় করে দেখানো হচ্ছে। তবে সশরীরে দেশে উপস্থিত থাকা আর প্রকৃত নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী হওয়া এক কথা নয়।
বিএনপি এখনো এই বিশ্বাস প্রচার করে যাচ্ছে যে, তারেক রহমানের উপস্থিতি পুরো রাজনৈতিক সমীকরণকে হঠাৎ বদলে দেবে। কিন্তু বাস্তবতা অনেক বেশি রূঢ়। বড় সিদ্ধান্তগুলো আসলে নেওয়া হচ্ছে রুদ্ধদ্বার কক্ষে, আইনি চেম্বারে, গোয়েন্দা পর্যালোচনায় এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের নিভৃত কলকব্জায়—যেসব অঙ্গনে বিএনপি কোনো প্রধান অংশ নয়, বরং কেবলই একটি সুবিধাজনক এবং পরিবর্তনযোগ্য ঘুঁটি মাত্র।
এখানে দাবার ছক সাজানো হচ্ছে, পাশা খেলা চলছে এবং প্রতিটি চাল অন্যদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। অথচ বিএনপি নেতারা ঠিক সেইসব মানুষের মতো আত্মবিশ্বাসের সাথে কথা বলছেন, যারা বিশ্বাস করেন যে তারা এখনই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন।
তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যাক যে, ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে বিএনপি কোনোভাবে সবচাইতে বেশি আসন নিয়ে জয়ী হলো। কিন্তু এই ফলাফল সংকট নিরসন করার পরিবর্তে আরও বড় ধরনের ঝড়ের জন্ম দেবে।
বর্তমান জোটের প্রধান অংশীদার—জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় নাগরিক পার্টির একাংশ এবং জুলাই আন্দোলনের চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলো বারবার প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে যে, তারা ১৯৭২ সালের সংবিধানের অধীনে শপথ নিতে অস্বীকার করবে। এই মৌলিক অঙ্গীকার ছাড়া কোনো সাংবিধানিকভাবে বৈধ সরকার গঠন করা সম্ভব নয়। একটি নির্বাচন হতে পারে, ভোট গণনা হতে পারে এবং আসনও বরাদ্দ হতে পারে, কিন্তু একটি কার্যকর ও স্বীকৃত প্রশাসন গঠনের পথ পুরোপুরি রুদ্ধ হয়ে থাকবে।
এই সাংবিধানিক অচলাবস্থার পাশাপাশি আরও এক অন্ধকারাচ্ছন্ন হুমকি ঘনীভূত হচ্ছে। রাজনৈতিক মহলে ক্রমাগত প্রতিবেদন আসছে যে, জুলাই অভ্যুত্থানের সময় গঠিত বিভিন্ন সশস্ত্র বা আধা-সশস্ত্র মিলিশিয়া সদৃশ বাহিনী এখন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সক্রিয়। যদি নির্বাচন পরবর্তী উত্তেজনা রাজপথের সহিংসতা, সংঘর্ষ, লুটপাট বা ব্যাপক বিশৃঙ্খলায় রূপ নেয়, তবে তাৎক্ষণিক প্রশ্নটি দাঁড়াবে: আসলে কে নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে?
এই দীর্ঘস্থায়ী বিশৃঙ্খলাকে এই অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা হতে পারে যে, “স্বাভাবিক ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য পরিস্থিতি অত্যন্ত অস্থিতিশীল। তখন ইউনূস নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী প্রশাসন যুক্তি দিতে পারে যে, গণপরিষদ প্রক্রিয়ার পুরোটা সময় সম্ভবত অনির্দিষ্টকালের জন্য তাদেরকেই ক্ষমতায় থাকতে হবে।
ইউনূসের রাষ্ট্রপতি হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা
সবচাইতে আশঙ্কাজনক এই পরিস্থিতির কেন্দ্রে রয়েছেন স্বয়ং ড. ইউনূস। একটি ক্রমবর্ধমান ভীতি ছড়িয়ে পড়ছে যে, তিনি পরিকল্পিতভাবে জামায়াতে ইসলামীকে এই জোটের অগ্রভাগে থাকা দল হিসেবে ব্যবহার করছেন এবং পর্দার আড়ালে নিজের দীর্ঘমেয়াদী ব্যক্তিগত লক্ষ্যকে এগিয়ে নিচ্ছেন। আর এই ব্যক্তিগত লক্ষ্য আমূল পুনর্গঠিত একটি শাসনব্যবস্থার অধীনে রাষ্ট্রপতি হওয়া।
রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার মধ্যে “ভারসাম্য” আনার যে বিষয়টি নিয়ে প্রচুর আলোচনা হচ্ছে, গভীরভাবে পরীক্ষা করলে তার একদম ভিন্ন একটি অর্থ বেরিয়ে আসে। প্রস্তাবিত বেশ কিছু মডেলে সশস্ত্র বাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থা এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ওপর কার্যকর কর্তৃত্ব প্রায় সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে, যা প্রধানমন্ত্রীকে কেবল একজন আলঙ্কারিক প্রধান বা নামসর্বস্ব ব্যক্তিত্বে পরিণত করবে।
এমন একটি কাঠামোতে তারেক রহমানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন কেবল পোস্টার, সংবাদ বিজ্ঞপ্তি এবং দলীয় প্রচারণার একটি ফাঁকা বুলি ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। কারণ এই ব্যবস্থায় কোনো অর্থবহ নির্বাহী ক্ষমতা থাকবে না।
ঠিক এই বিশাল ঝুঁকির কারণেই আওয়ামী লীগ এবং কার্যত প্রতিটি প্রধান মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষীয় রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম ১২ ফেব্রুয়ারির এই নির্বাচন প্রক্রিয়াকে সরাসরি বর্জন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
তাদের অবস্থান স্পষ্ট এবং অনড়। বাংলাদেশী জাতির একমাত্র বৈধ ভিত্তিগত সংগ্রাম হলো ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ। ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থান—তা যত শক্তিশালী বা আবেগপ্রসূতই হোক না কেন এটি দ্বিতীয় স্বাধীনতা হতে পারে না এবং হওয়া সম্ভবও নয়। যারা ২০২৪-কে চূড়ান্ত “মুক্তি”র মুহূর্ত হিসেবে গণ্য করার জেদ ধরছে, তারা কার্যত সেই আদর্শিক বিরোধিতারই ধারাবাহিকতা বজায় রাখছে যা তারা ১৯৭১ সালে পোষণ করেছিল। মানসিকভাবে এবং রাজনৈতিকভাবে তারা এমন এক বিশ্বদর্শনে নোঙর ফেলে আছে যা ১৯৭১ সালের পূর্ব পাকিস্তানের কাছাকাছি।
এই আদর্শিক বিভাজন বাংলাদেশি সমাজকে তার একেবারে ভিত্তিমূলে ভেঙে দেওয়ার হুমকি তৈরি করছে। যখন একটি জাতির জন্মকথা ও ইতিহাস নিয়ে সর্বসম্মত ঐক্য ভেঙে পড়ে, তখন রাষ্ট্রের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই ক্রমে দুর্বল ও অনিশ্চিত হয়ে ওঠে। সেই শূন্যতার মধ্যেই জন্ম নেয় দীর্ঘমেয়াদি ও জবাবদিহিহীন ক্ষমতা কুক্ষিগত করার সুযোগ।
এখন আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সেই কঠোর ও মৌলিক প্রশ্নটি। রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত প্রচারণা, ইতিহাস সংশোধন এবং সাংবিধানিক কারসাজির এই জটিল জালের ভেতর দিয়ে কি বিএনপির সরকার গঠনের স্বপ্ন আদৌ বাস্তবায়িত হতে পারে? নাকি আমরা আবারও সেই চেনা দৃশ্যের মুখোমুখি হব—যেখানে আকাশচুম্বী প্রত্যাশার পর আবার উপলব্ধি হবে যে প্রকৃত ক্ষমতা আসলে কখনোই হাতবদল হয়নি?
ড. মুহাম্মদ ইউনুস, যিনি একসময় ক্ষুদ্রঋণ ও দারিদ্র্য বিমোচনের পথিকৃৎ হিসেবে বিশ্বজুড়ে সম্মানিত ছিলেন, আজ তাকে দেখা যাচ্ছে একটি সুপরিকল্পিত, কারসাজিপূর্ণ ও গণতন্ত্রবিরোধী প্রকল্পের মুখ্য রূপকার হিসেবে। তার নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী শাসন কোনো নিরপেক্ষ কেয়ারটেকার সরকারের ভূমিকা পালন করেনি। বরং এটি আগ্রাসীভাবে নির্বাচনী পরিসরকে একতরফা করে তুলেছে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরোধী শক্তিকে ক্ষমতাবান করেছে, সামাজিক বিভাজনকে আরও গভীর করেছে । পাশপাশি সম্ভাব্য অরাজকতা থেকে ফায়দা তোলার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রেখেছে।
১২ ফেব্রুয়ারির আনুষ্ঠানিক ফলাফল যাই হোক না কেন, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, জাতীয় পরিচয় এবং সামষ্টিক স্মৃতির ওপর যে গভীর আঘাত হানা হচ্ছে, তা থেকে পুনরুদ্ধার হতে কয়েক দশক—এমনকি একাধিক প্রজন্মও লেগে যেতে পারে।
বাংলাদেশের মানুষ এমন ছায়া-সরকার, পরিকল্পিত বয়ান এবং একজন অনির্বাচিত ব্যক্তির অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার অধীনে শাসিত হওয়ার চেয়ে বহুগুণ ভালো ও মর্যাদাপূর্ণ শাসনব্যবস্থার দাবিদার।