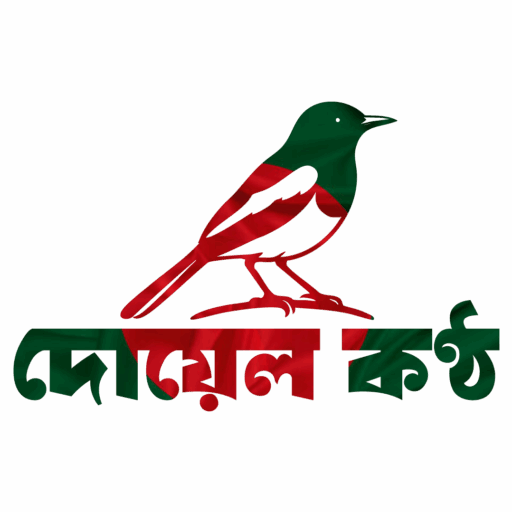আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে যতটা না আলোচনা হচ্ছে ভোট বা সরকার গঠন নিয়ে, তার চেয়েও বেশি প্রশ্ন উঠছে নির্বাচনের পর প্রকৃত ক্ষমতা কার হাতে থাকবে—এই বিষয়টি নিয়ে। অন্তর্বর্তী সরকার ঘোষিত গণভোট, জুলাই জাতীয় সনদ এবং ‘সংবিধান সংস্কার পরিষদ’–এর ধারণা মিলিয়ে বাংলাদেশের সাংবিধানিক কাঠামোর ভেতরে এক অভূতপূর্ব ও বিপজ্জনক অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।
জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, এই নির্বাচন অতীতের কোনো নির্বাচনের মতো নয়। কারণ, এই নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সংসদ শুধু সরকার পরিচালনাই করবে না, বরং একইসাথে ১৮০ দিন ‘সংবিধান সংস্কার পরিষদ’ হিসেবেও কাজ করবে।
সংবিধান সংস্কার পরিষদ: সংসদের ওপর আরেক সংসদ?
গণভোটে ‘হ্যাঁ’ সূচক হলে যে ব্যবস্থা কার্যকর হবে, তাতে বলা হচ্ছে— নির্বাচিত সংসদ সদস্যরাই আবার আলাদা শপথ নিয়ে একটি সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠন করবেন, যাদের হাতে থাকবে সংবিধান সংশোধনের পূর্ণ ক্ষমতা বা তথাকথিত ‘কনস্টিটিউয়েন্ট পাওয়ার’।
কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধানে এমন কোনো দ্বৈত ভূমিকার ধারণা নেই। সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা কেবল জাতীয় সংসদের, কোনো আলাদা পরিষদের নয়।
তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে— যদি সংসদই সব ক্ষমতার মালিক হয়, তবে আবার আলাদা করে সংবিধান সংস্কার পরিষদের প্রয়োজন কেন? আর যদি পরিষদই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়, তবে সংসদ ও সরকার থাকবে কোন অবস্থানে?
সরকার গঠন হবে, কিন্তু ক্ষমতা থাকবে কার হাতে?
এই কাঠামোর সবচেয়ে গুরুতর দিক হলো— নির্বাচনের পর সরকার গঠন হলেও ১৮০ দিন ধরে সংবিধান সংস্কার চলবে। এই সময়ে প্রধানমন্ত্রী থাকবেন, মন্ত্রিসভা থাকবে, বাজেট হবে। কিন্তু একইসাথে রাষ্ট্রের মৌলিক কাঠামো পরিবর্তনের ক্ষমতা থাকবে অন্য একটি পরিচয়ের হাতে—সংবিধান সংস্কার পরিষদের। এটি কার্যত একটি ক্ষমতা দ্বিখণ্ডনের অবস্থা, যেখানে নির্বাচিত সরকার থাকবে নামমাত্র, আর প্রকৃত ক্ষমতা থাকবে সাংবিধানিক পুনর্গঠনের নামে জারি করা আদেশ ও নির্দেশনার ভেতরে।
বিএনপি জিতলেও কি সরকার চালাতে পারবে?
রাজনৈতিক বাস্তবতায় ধরে নেওয়া যাক, এই নির্বাচনে বিএনপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। তাহলে কি তারা স্বাধীনভাবে সরকার গঠন ও পরিচালনা করতে পারবে? এই প্রশ্নের উত্তর ক্রমশ ‘না’-এর দিকেই ঝুঁকছে।
কারণ— বিএনপি ইতোমধ্যে জুলাই জাতীয় সনদে স্বাক্ষর করেছে। গণভোটে ‘হ্যাঁ’ হলে সনদের সাংবিধানিক সংস্কার বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। নতুন সংবিধান কার্যকর হলে সরকারকে আবার নতুন কাঠামোয় শপথ নিতে হবে। এর অর্থ দাঁড়ায়, জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকারও থাকবে আগাম নির্ধারিত সংস্কারের শর্তে আবদ্ধ।
রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি: সংস্কার না ক্ষমতার কেন্দ্রায়ন?
জুলাই সনদের একটি বড় দিক হলো রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা সীমিত করার আলোচনা।এখানে একটি সুস্পষ্ট রাজনৈতিক নকশা দেখা যাচ্ছে— রাষ্ট্রপতির আদেশে নির্বাহী সিদ্ধান্ত। প্রধানমন্ত্রীকে সীমিত প্রশাসনিক ভূমিকায় নামিয়ে আনা। এই পরিবর্তন বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ কার্যত সংসদীয় ব্যবস্থা থেকে সরে গিয়ে এক ধরনের রাষ্ট্রপতিনির্ভর নির্বাহী কাঠামোর দিকে চলে যাবে, যার গণতান্ত্রিক বৈধতা নিয়ে বড় প্রশ্ন থাকবে।
গণভোট: সাংবিধানিক বৈধতা কোথায়?
সবচেয়ে বড় বিতর্কের জায়গা হলো গণভোট নিজেই। বাংলাদেশের সংবিধানে— জাতীয় পর্যায়ে গণভোট আয়োজনের কোনো স্পষ্ট বিধান নেই; গণভোটের ফল বাধ্যতামূলক কি না, তারও নির্দেশনা নেই। সংবিধান সংশোধনের একমাত্র বৈধ পথ সংসদ। অথচ সংসদের ওপরেই গণভোটের মাধ্যমে একটি পূর্বশর্ত চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।এটি প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার একটি প্রচেষ্টা, যা সংবিধানের মৌলিক দর্শনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।
জামায়াত–ইউনূস সমীকরণ ও প্রশাসনিক বাস্তবতা
রাজনৈতিক অঙ্গনে আরও একটি আলোচিত বিষয় হলো—প্রশাসন ও নির্বাহী বিভাগে জামায়াতপন্থী প্রভাব।এই বাস্তবতায় বিএনপির নির্বাচনে জয় পাওয়ার সম্ভাবনাকেই অনেকেই “আকাশকুসুম স্বপ্ন” বলে অভিহিত করছেন। অথচ গণভোটে ‘হ্যাঁ’ প্রচারণা চালানো হচ্ছে পূর্ণ শক্তিতে, যেখানে বিএনপি নেতৃত্ব রাজনৈতিক চাপ ও পূর্বস্বাক্ষরের দায়ে কার্যত কোণঠাসা।
সংস্কারের নামে বৈধতার সন্ধান?
সব মিলিয়ে প্রশ্ন দাঁড়ায়—এই গণভোট কি সত্যিই গণতন্ত্র শক্তিশালী করার জন্য, নাকি এটি একটি নির্বাচিত সরকারকে আগেই নিয়ন্ত্রণে রাখার সাংবিধানিক কৌশল? নির্বাচন দিয়ে সরকার আনা হলেও যদি ক্ষমতা থাকে আদেশ, সনদ ও পরিষদের হাতে— তবে সেটি গণতন্ত্র নয়, বরং নিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার নতুন সংস্করণ।
দিনশেষে আশঙ্কা একটাই— গণভোটের ‘হ্যাঁ’ মানে হয়তো জনগণের সম্মতি নয়, বরং ভবিষ্যৎ সরকারগুলোর ওপর স্থায়ী নিয়ন্ত্রণের বৈধ কাগজ।