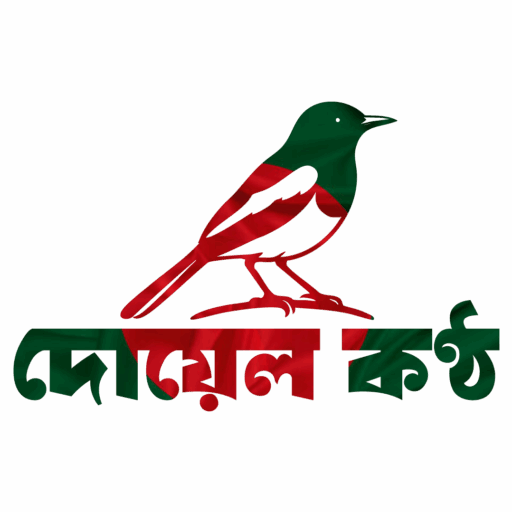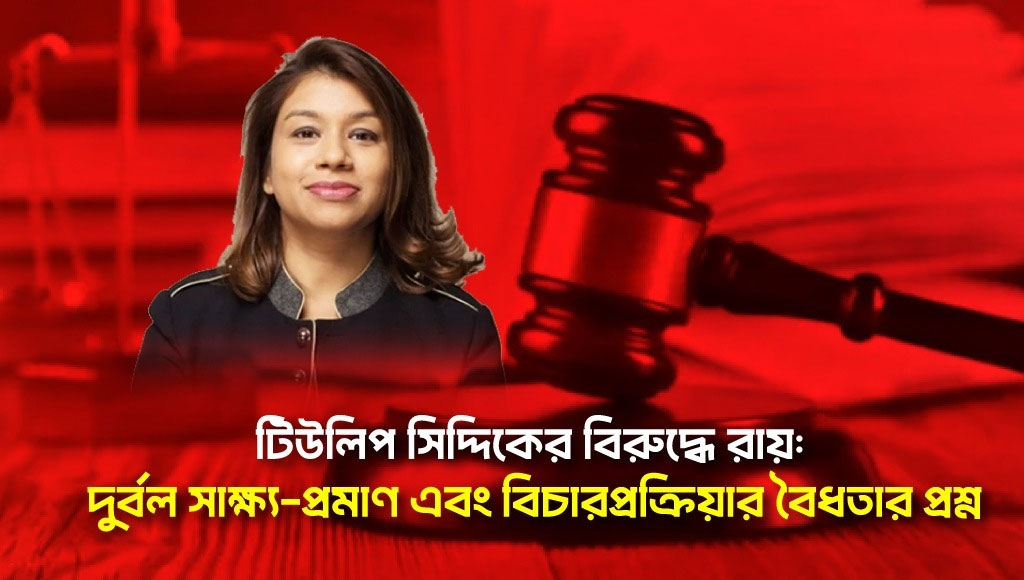সম্প্রতি গণমাধ্যমে টিউলিপ সিদ্দিকের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে একটি আদালতের দেওয়া রায় নিয়ে নানা প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে। টিউলিপ যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্ট সদস্য এবং বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাতনি। একজন আইন বিশেষজ্ঞ হিসেবে এ বিষয়ে আমার মতামত প্রকাশ করা প্রয়োজন মনে করছি।
এই লেখায় আমি টিউলিপ সিদ্দিকের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলায় কীভাবে অন্যায় করা হয়েছে, তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব। প্রথমেই স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা দরকার— এই মামলায় ন্যায্য বিচার এবং যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার আন্তর্জাতিক মান মারাত্মকভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। টিউলিপ সিদ্দিকের বিরুদ্ধে যে বিচারকার্য পরিচালিত হয়েছে, তা বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৫ অনুচ্ছেদ এবং আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সনদ (আইসিসিপিআর) ১৯৬৬-এর ১৪ অনুচ্ছেদের সুস্পষ্ট বিরোধী।
এই লঙ্ঘনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— আইনজীবী দিয়ে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, বিবাদী পক্ষের সাক্ষী উপস্থাপনের সুযোগ না দেওয়া, জেরা করার অধিকার সীমিত করে দেওয়া এবং সন্দেহজনক ও জাল-জালিয়াতির অভিযোগ থাকা প্রমাণের ওপর নির্ভর করা।
এ ধরনের মৌলিক ত্রুটি ও অনিয়ম দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের আলোকে পুরো বিচারপ্রক্রিয়াকেই বাতিলযোগ্য করে তোলে। সরকারপক্ষ দাবি করেছে যে আদালতে উপস্থাপিত তথ্য-প্রমাণ থেকে নাকি প্রমাণিত হয়েছে টিউলিপ সিদ্দিক তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক ব্যবহার করে নিজের পরিবারের জন্য রাষ্ট্রীয় জমি দখল করেছেন।
মূল প্রশ্ন হলো। এই অভিযোগটি কি বাংলাদেশের ফৌজদারি মানদণ্ড অনুযায়ী যথেষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে? ফৌজদারিতে একটি মৌলিক নীতি হলো: কোনো অভিযুক্তকে দণ্ড দেওয়া যাবে কেবল তখনই, যখন অপরাধটি “যাবতীয় যৌক্তিক সন্দেহ”এর ওপরে প্রমাণিত হয়।সামান্যতম সন্দেহ থাকলেই খালাস দিতে হয় — কারণ ফৌজদারি শাস্তি মানুষের স্বাধীনতা, সম্পদ, সম্মান এবং এমনকি জীবনই কেড়ে নিতে পারে। আইনের ঐতিহ্যবাহী নৈতিক আদেশটি বলছে: “দশজন অপরাধী থাকুক, কিন্তু একজন নির্দোষ যেন ভুলক্রমে দণ্ডিত না হয়।”
সরকারপক্ষের দাবি ছিল, টিউলিপ সিদ্দিক তার খালা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা ব্যবহার করে নিজের মা শেখ রেহানার জন্য রাষ্ট্রীয় জমি বরাদ্দ করিয়েছেন। রায়ে বলা হয়েছে। টিউলিপ মোবাইল, হোয়াটসঅ্যাপ ও বিভিন্ন ইন্টারনেট অ্যাপের মাধ্যমে এবং বাংলাদেশ আসার সময় সরাসরি সাক্ষাতে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর একান্ত সচিব সালাউদ্দিনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন; দুইজন গণভবন কর্মকর্তা এই কথার সমর্থক সাক্ষ্য দিয়েছেন।
গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এই অভিযোগে স্পষ্ট তথ্যগত ও প্রমাণগত ত্রুটি আছে। প্রথমত, “প্রভাব প্রয়োগ করে জমি বরাদ্দ করানো”—এই কৌশলগত ধারণাটি যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ যে ব্যক্তি সুবিধাভোগীর নাম বলা হয়েছে (শেখ রেহানা) তিনি প্রধানমন্ত্রীরই বোন; দুই বোনের মধ্যে ঘন ও নিয়মিত যোগাযোগ স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত। উপরন্তু, ব্রিটিশ পার্লামেন্টে নির্বাচিত হওয়ার পর টিউলিপ সিদ্দিকের বাংলাদেশে সরাসরি যাতায়াতও সীমিত। এসব বাস্তবতা বিবেচনায় নিলে সরকারপক্ষের দাবি যথেষ্ট যৌক্তিকতা পায় না। ফৌজদারি প্রমাণের কঠোর মানদণ্ডের আলোকেই এই পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা ও সীমিত যোগাযোগকে সামনে রেখে যে তত্ত্বটি দাড় করানো হয়েছে মারাত্মকভাবে তা দুর্বল।
দ্বিতীয়ত, গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এক ব্রিটিশ সাংবাদিক যখন সরকারি কৌঁসুলিকে প্রশ্ন করেন টিউলিপ সিদ্দিকের হোয়াটসঅ্যাপ বা অন্য কোনো ইন্টারনেটভিত্তিক যোগাযোগের কোনো রেকর্ড আদালতে উপস্থাপন করা হয়েছে কি না? তখন কৌঁসুলি কোনো সুস্পষ্ট বা সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেননি। অথচ পুরো মামলাটি দাঁড়িয়ে আছে মূলত এই কথিত যোগাযোগের ওপর। ফলে এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণের অনুপস্থিতি মামলার বিশ্বাসযোগ্যতায় মারাত্মক আঘাত হানে।
তৃতীয়ত, সরকারপক্ষ গণভবনের দুজন কর্মকর্তাকে সাক্ষী হিসেবে হাজির করেছে। কিন্তু এখানে একটি স্বাভাবিক প্রশ্ন ওঠে: প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর ভাগ্নির মধ্যে হোয়াটসঅ্যাপ, অন্যান্য অ্যাপ কিংবা মুখোমুখি যে কথাবার্তা হওয়ার কথা বলা হয়েছে সে বিষয়ে গণভবনের কর্মচারীরা কীভাবে অবগত হবেন? রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে পারিবারিক বা ব্যক্তিগত আলোচনা তো কর্মচারীদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয় না। সুতরাং এ ধরনের সাক্ষ্য স্বভাবতই সন্দেহজনক ও গ্রহণযোগ্যতার দিক থেকে দুর্বল।
চতুর্থত, ২০২২ সালে টিউলিপ সিদ্দিক বাংলাদেশে এসে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর একান্ত সচিবকে প্রভাবিত করেছেন সরকারপক্ষের এই দাবি বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। নির্ভরযোগ্য রেকর্ড থেকে স্পষ্ট হয় যে ২০২২ সালে টিউলিপ সিদ্দিক একবারও বাংলাদেশে আসেননি। অর্থাৎ মামলার অন্যতম প্রধান তথ্যগত ভিত্তিই এখানেই ভেঙে পড়ে।
ওপরের সব যুক্তি একত্রে বিবেচনা করলে স্পষ্ট হয় যে টিউলিপ সিদ্দিকের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ফৌজদারি আইনের প্রয়োজনীয় প্রমাণের মানদণ্ডে কোথাও দাঁড়ায় না। অপরাধের মৌলিক উপাদান প্রমাণ করতে ব্যর্থ হওয়া, অনুমাননির্ভর ও অবিশ্বাস্য সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করা, এবং যোগাযোগ বা প্রভাব বিস্তারের কোনো নির্ভরযোগ্য দলিল–দস্তাবেজ আদালতে পেশ না করার ঘটনা আইনগতভাবে টেকসই হতে পারে না।
কিছু সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হয়েছে যে বিতর্কিত জমিটি ঢাকার সবচেয়ে ব্যয়বহুল আবাসিক এলাকা গুলশান–২–এ অবস্থিত, যেখানে সম্পত্তির দাম বিশ্বের বড় বড় শহরের সঙ্গেও পাল্লা দেয়। এই তথ্য সম্পূর্ণ ভুল।
মামলায় যে প্লটটির কথা বলা হচ্ছে, তা আসলে পূর্বাচলে অবস্থিত—ঢাকার পাশে সরকারের একটি নতুন আবাসিক প্রকল্প। এখানে সরকার নির্ধারিত মূল্যে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের জন্য—মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্তদের জন্যও—প্লট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পটির মোট আয়তন প্রায় ৬,২১৩ একর (২৫.১৪ বর্গকিলোমিটার)।
পূর্বাচল এখনো ঘনবসতিপূর্ণ আবাসিক এলাকায় পরিণত হয়নি; ফলে এখানকার প্লটের বাজারমূল্য তুলনামূলকভাবে কম। মামলার প্লটটির বাজারমূল্য সর্বোচ্চ পাঁচ থেকে ছয় কোটি টাকার মতো হতে পারে। অথচ একই আয়তনের জমি যদি গুলশান–২–এ হতো, তার দাম হতো প্রায় ১০০ কোটি টাকা।
এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখযোগ্য। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দুই কন্যার বিরুদ্ধে কম দামের সরকারি জমি বরাদ্দ নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ আনা হলেও বাস্তবতা ভিন্ন। বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্য হিসেবে তারা নিজেদের ঐতিহাসিক ও উচ্চমূল্যের সম্পত্তির ব্যাপারে যে আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তা সুস্পষ্ট।
ধানমন্ডি–৩২ নম্বরের ঐতিহাসিক বঙ্গবন্ধু ভবন যার বর্তমান বাজারমূল্য ৩০০ কোটি টাকার বেশি দুই বোন জাতির জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে জাদুঘরে রূপান্তরের উদ্দেশ্যে দান করেছেন।
এছাড়া ছোট বোন শেখ রেহানার ধানমন্ডির একটি বাড়ি ২০০১ সালের নির্বাচনের পর বিএনপি–জামায়াত জোট সরকার অবৈধভাবে দখল করে নিয়েছিল। পরে মামলার মাধ্যমে তিনি সেই সম্পত্তি ফিরে পান। কিন্তু ব্যক্তিগত লাভের জন্য বিক্রি না করে— যার মূল্য ২০০ কোটি টাকারও বেশি—তিনি সেটি বাংলাদেশ পুলিশের নামে নিবন্ধন করে রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ দান করেন। চাইলে তিনি সেই বাড়িটি পুলিশসহ যেকোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে বিপুল অর্থে বিক্রি করতে পারতেন, কিন্তু ব্যক্তিগত আর্থিক সুবিধার পথে না গিয়ে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে সেটি উৎসর্গ করেছেন।